বইয়ের নাম: কপালকুন্ডলা
লেখকের নাম: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশকাল: ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ
কপালকুন্ডলা উপন্যাস – ঊনিশ শতকের গোড়াতে বাংলা গদ্য সাহিত্যের নবযুগের সূচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কপালকুন্ডলা (১৮৬৬) তার সৃজনশীল প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। এটি বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় স্বার্থক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত এবং এর বুননশৈলী ও ভাবগম্ভীরতা একে রোমান্টিক ও রহস্যময় সাহিত্যকর্মের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
Table of Contents
কপালকুন্ডলা উপন্যাসের কাহিনী ও বিশ্লেষণ
কপালকুন্ডলা উপন্যাসের কাহিনী অরণ্যে বাস করা এক রহস্যময় নারী কপালকুন্ডলাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। এই নারী এক কাপালিকের আশ্রয়ে বড় হয়েছে, যা তার জীবনকে এক রহস্যময় আবহে আবৃত করেছে। সমাজ সংস্কারের সঙ্গে অপরিচিতা এই নারীর নবকুমারের সাথে বিবাহ এবং সমাজের সাথে তার দ্বন্দ্বই এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য।
উপন্যাসের সূচনা হয় তীর্থযাত্রীদের নৌকা পথ হারিয়ে এক জনবিচ্ছিন্ন স্থানে পৌঁছানোর মাধ্যমে। নবকুমার কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে বনে আটকে পড়ে, আর তখনই তার সাক্ষাৎ হয় এক কাপালিকের সাথে, যে তাকে বলি দিতে চায়। কিন্তু কাপালিকের পালিতা কন্যা কপালকুন্ডলার সহায়তায় নবকুমার পালিয়ে যায়। পরে, কপালকুন্ডলাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে নবকুমার সমাজে ফেরার সিদ্ধান্ত নেয়।
এরপর শুরু হয় নতুন দ্বন্দ্ব। নবকুমারের পূর্বতন স্ত্রী মতি, যে ধর্মান্তরিত হয়ে আগ্রায় চলে যায়, ঘটনাক্রমে কপালকুন্ডলার সাথে দেখা পায়। সে নবকুমারের জীবনে পুনরায় প্রবেশ করতে চায় এবং কপালকুন্ডলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। অন্যদিকে, কাপালিকও প্রতিশোধ নিতে কপালকুন্ডলাকে বলির জন্য নিয়ে যেতে চায়। মতি এবং কাপালিকের চক্রান্তে কপালকুন্ডলা এক সময় নবকুমারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। উপন্যাসের শেষ পরিণতি বিষাদময়—কপালকুন্ডলা এক স্রোতময় নদীতে হারিয়ে যায়, আর নবকুমার তাকে খুঁজতে গিয়ে নদীতে নেমে পড়ে। কেউ আর ফিরে আসে না, যা উপন্যাসের ট্রাজিক পরিণতি হিসেবে চিত্রিত হয়েছে।
উপন্যাসের শৈলী ও সাহিত্যিক গুরুত্ব
‘কপালকুন্ডলা’ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক ও কল্পিত কাহিনীর সমন্বয়ে এক অনন্য রোমান্টিক আবহ সৃষ্টি করেছেন। একদিকে আছে সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলের আগ্রা নগরী ও তার ঐতিহাসিক স্থাপত্য, অন্যদিকে রহস্যময় অরণ্য ও সমুদ্রতীর।
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও রহস্যময়তার অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। তিনি প্রকৃতিকে নিছক পটভূমি হিসেবে নয়, বরং এক জীবন্ত চরিত্রের মতো উপস্থাপন করেছেন। কপালকুন্ডলার চারিত্রিক গভীরতা ও তার স্বাধীনচেতা মনোভাব এই উপন্যাসকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। একইসাথে, সমাজব্যবস্থার সংকীর্ণতা এবং নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রশ্ন তুলেছেন, তা উপন্যাসটিকে সময়োপযোগী করে তুলেছে।
উপসংহার
‘কপালকুন্ডলা’ বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। এর কাহিনী বিন্যাস, চরিত্র চিত্রণ এবং ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক উপাদানের সংমিশ্রণ বাংলা উপন্যাসকে নতুন মাত্রায় নিয়ে গেছে। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রদান করেন এবং পরবর্তীকালে দামোদর মুখোপাধ্যায় ‘মৃন্ময়ী’ শিরোনামে এই উপন্যাসের এক বিকল্প উপসংহার রচনা করেন।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন খুলনা জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তখন তিনি খুলনার জেলা প্রশাসকের বাসভবনের কাছে অবস্থিত এক ঐতিহাসিক বকুল গাছের নিচে বসে ‘কপালকুন্ডলা’ উপন্যাসের বেশ কয়েকটি অধ্যায় রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই গাছটি কালবৈশাখী ঝড়ে নষ্ট হয়ে যায়, তবে তার সাহিত্যিক ঐতিহ্য আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘কপালকুন্ডলা’ শুধু বাংলা সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ নয়, এটি বাংলা উপন্যাসের শৈল্পিক উৎকর্ষেরও অন্যতম উজ্জ্বল উদাহরণ।
লেখক পরিচিতি (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যিক। তিনি আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পথিকৃৎ হিসেবে পরিচিত। ১৮৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন।
তার সাহিত্যকর্মের মধ্যে “দুর্গেশনন্দিনী” (১৮৬৫) বাংলা ভাষায় প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। “আনন্দমঠ” (১৮৮২) উপন্যাসের “বন্দে মাতরম” গানটি ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। অন্যান্য জনপ্রিয় উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে “কপালকুণ্ডলা” (১৮৬৬), “মৃণালিনী” (১৮৬৯), “চন্দ্রশেখর” (১৮৭৭) ও “রাজসিংহ” (১৮৮১)।
তিনি সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি ধর্ম ও দর্শন নিয়েও লিখেছেন। তার “কৃষ্ণচরিত্র” গ্রন্থ হিন্দুধর্ম ও ঐতিহ্যের গভীর বিশ্লেষণ প্রকাশ করে। বাংলা ভাষাকে সহজ ও সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। তিনি এমন এক সময় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করা শুরু করেছিলেন, যখন বাঙ্গালীরা সবেমাত্র উচ্চ শিক্ষার দিকে গভীর মনোযোগ দিচ্ছে।
১৮৯৪ সালের ৮ এপ্রিল তিনি প্রয়াত হন। তার সাহিত্যকর্ম ভারতীয় জাতিসত্তা গঠনে অসামান্য অবদান রেখেছে এবং আজও পাঠকদের অনুপ্রাণিত করে।
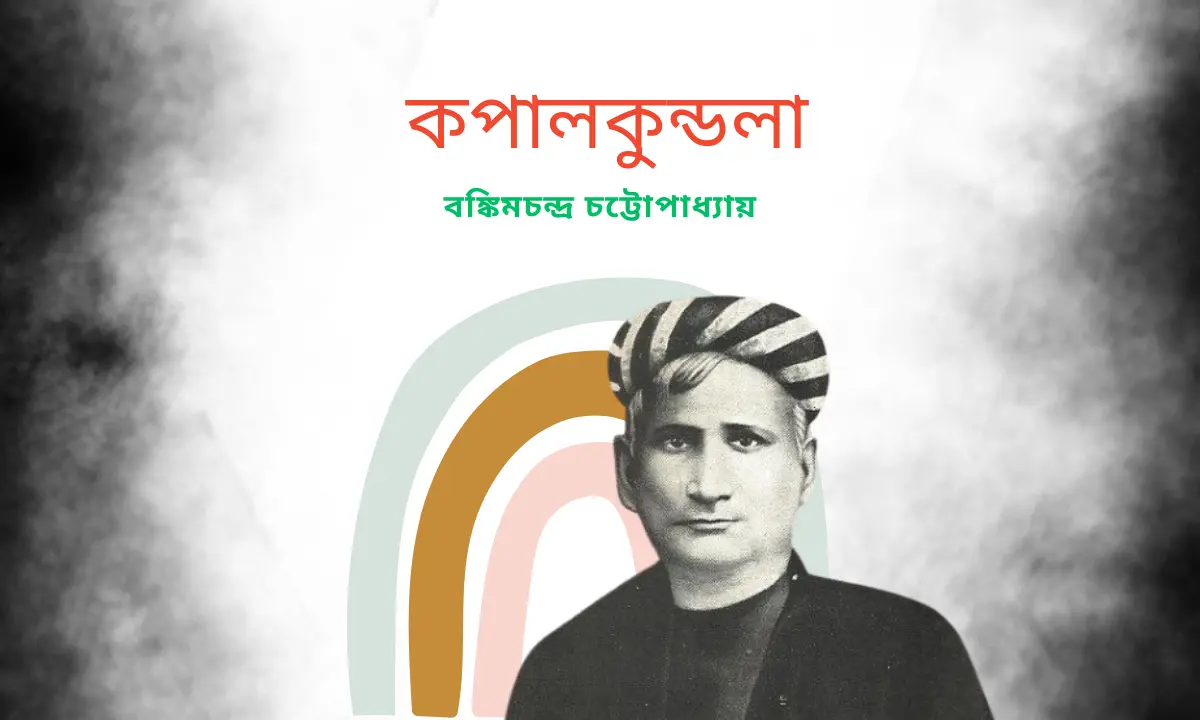
1 thought on “কপালকুন্ডলা উপন্যাসের সমালোচনা-1866”